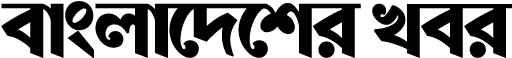প্রকৃতির লীলাভূমি আমাদের প্রিয় স্বদেশ, যা সকলের কাছে অপরূপ এবং বৈচিত্র্যময়। এখানে রয়েছে হাজারো শীতল ছায়াঘেরা গ্রাম, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যেমন- সাঁওতাল, উরাও, মাল পাহাড়িয়া, মাহালী, মুন্ডা, রাজোয়ারসহ অনেক জাতিসত্তা। যাদের নিজস্ব ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্য রয়েছে, যার ফলে বাঙালি সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।
বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩(ক) ধারায় যাদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে উপজাতিরা নিজেদের ‘আদিবাসী’ পরিচয় দিতে অধিকতর পছন্দ করে থাকেন। তাই উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী শব্দগুলো ব্যবহার না করে তারা সরাসরি আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করে।
বাংলা একাডেমির অভিধানে ‘আদিবাসী’ বলতে আদিম অধিবাসীদেরই আদিবাসী হিসেবে বোঝানো হয়েছে। আদিবাসী ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, আদিবাসী/উপজাতি জনগোষ্ঠী বলতে এমন সব জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা প্রাচীন কাল থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে পাওয়া ভূমিতে উত্তরাধিকার সূত্রে বসবাস করে আসছে। এরা নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল, যাদের নিজস্ব ভাষা ও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রয়েছে যা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক চিহ্নিত করেছে। আদিবাসীরা বাঙালি নয়, তবে বাংলাদেশি। সরকারি গেজেটে বাংলাদেশে প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বসবাস।
জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২২, প্রাথমিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের মোট সংখ্যা হলো ১৬,৫০,১৫৯ জন। ভৌগোলিকভাবে আদিবাসীরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত :
১. পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী, যেমন- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো প্রভৃতি এবং
২. সমতলে বসবাসরত আদিবাসী, যেমন- সাঁওতাল, উরাও, মাহালী, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি।
দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সমতলের আদিবাসীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। উত্তরবঙ্গে রাজশাহীর ব্যাপারে ১৮৭২ সালের এক জরিপে আদিবাসীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২০৭৬ জন (Hunter : 1872 Census)। তার মানে এই অঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাসের ইতিহাস অনেক প্রাচীন।
কাজ, খাদ্যের তাগিদ বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের আগমনটাও অনেকটা এমনই। ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী নীল চাষের জন্য বেশ পরিচিত ছিল। সমতলের আদিবাসীদের বিরাট একটা অংশের বসবাস উত্তরবঙ্গে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর জরিপ অনুযায়ী আদিবাসীরা ৭০-৯০ শতাংশ ভূমিহীন। ১০ শতাংশ মানুষের নিজস্ব জমিজমা আছে। অর্থাৎ অধিকাংশ আদিবাসী জনগণের বসত গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের খাস জমি বা অন্যের জমির উপর। তবে আদিবাসীরা বিক্ষিপ্তভাবে নয় বরং একসাথে থাকতে পছন্দ করেন।
এজন্য আদিবাসী গ্রামগুলোতে শুধু আদিবাসীদের বসতভিটা চোখে পড়বে। আদিবাসীদের সামাজিক প্রশাসনিক কাঠামোগুলো খুবই উন্নত এবং প্রাচীনকাল থেকেই অনেক উন্নত ও গণতান্ত্রিক। এজন্য আদিবাসীরা তাদের সমস্যাগুলোর বেশিরভাগ সমাধান পায় গ্রাম্য প্রশাসন থেকে। তবে বর্তমানে আদিবাসীদের জন্য পৃথক কোন মন্ত্রণালয় না থাকার কারণে ভূমির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। আদিবাসীদের সরলতা, অজ্ঞতা, অক্ষরজ্ঞানের অভাবে জমিজমা বিভিন্ন কায়দায় তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন মহল। বিগত বছরগুলোতে ভূমিদস্যুদের কাছে অনেক আদিবাসী ভূমিহীন হয়েছে। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং অধিগ্রহণ তো আছে। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে জমি বন্ধক রেখে সেটা অর্থের অভাবে আর ফিরে না পাওয়া তো আছে। অনেক সময় আদিবাসীরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। যেটি দেখার কেউ নেই।
থানা বা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ বা মামলার ক্ষেত্রে হয়রানি করা হয়। শোষিত আদিবাসীদের পক্ষে রায় হয় না। অ-আদিবাসীরা তাদের কাজে, কথায়, ব্যবহারে সবসময় খারাপ আচরণ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে। স্থানীয় বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে আদিবাসীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। যার ফলে সমাজ উন্নয়নে আদিবাসীদের মেধা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা প্রয়োগে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। অধিকাংশ আদিবাসীরা প্রধানত দুটো ধর্মের অনুসারী। ১. তাদের আদি ধর্ম (আদিবাসীদের আদি ধর্ম বলতে প্রকৃতি পূজা, যেখানে কোন ধরনের মূর্তি পূজার কোন অবকাশ নেই) ও ২. উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। আবার অনেকে হিন্দু ধর্মের অনুসারী। তবে যে কোন ধর্মই পালন করুক না কেন, সে আদিবাসী। কেননা জাতি এবং ধর্ম এই দুটি বিষয় আলাদা হলেও, পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।
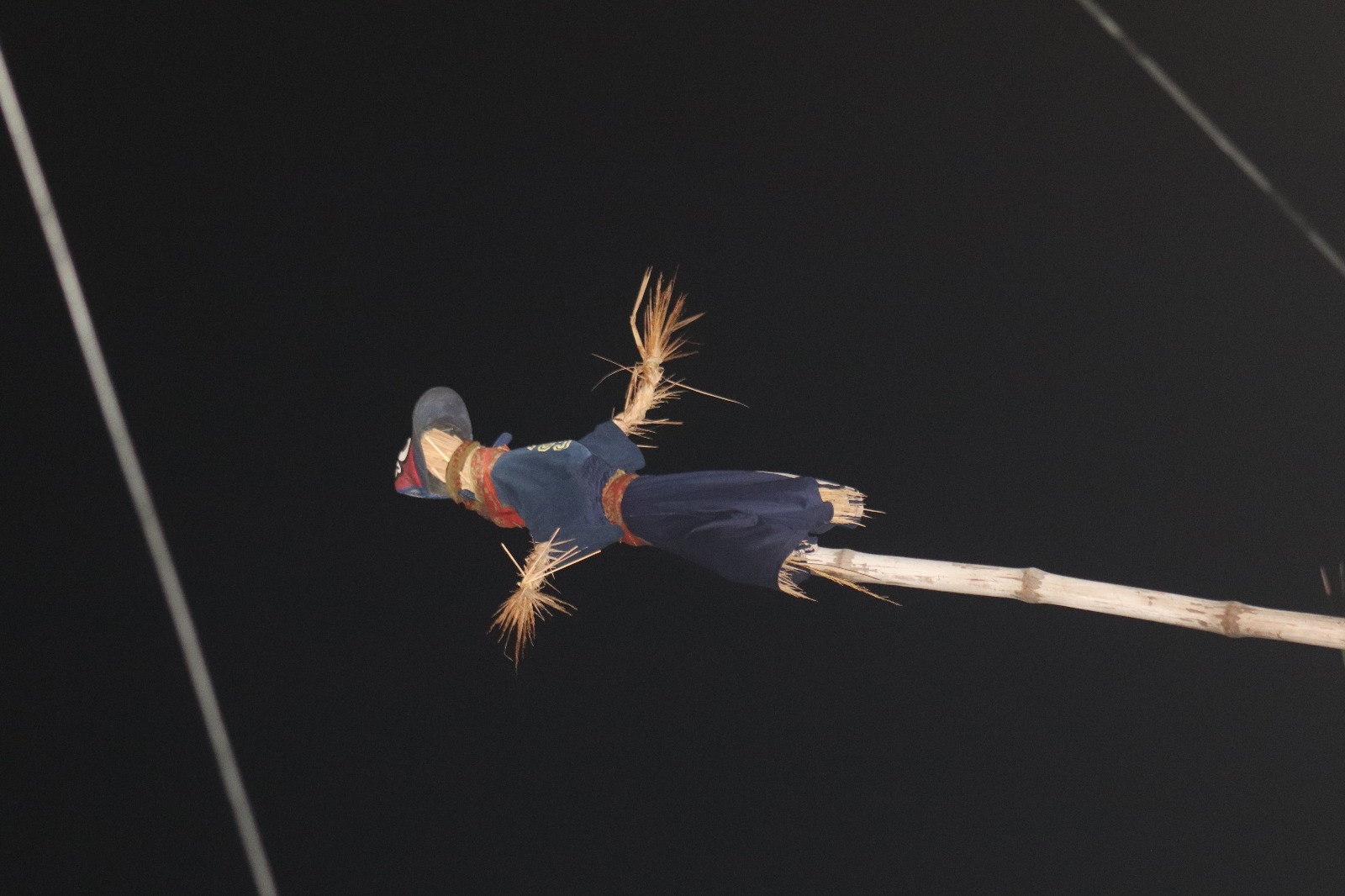
ভাষা একটি জাতি বা সংস্কৃতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন একটি জাতিকে নিঃশেষ করতে হলে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না; যদি তাদের ভাষা হারিয়ে যায়। আদিবাসীদেরও নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, সমতলের অধিকাংশ আদিবাসীদের ভাষার নিজস্ব লিখিত রূপ না থাকলেও, বছরের পর বছর আজও টিকে আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র ভাষা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উড়াওরা ‘কুড়ুখ’ এবং ‘সাদরি’ দুটি ভাষায় কথা বলে।
অন্যদিকে মাহালীরা আবার গোত্রভেদে আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে। আমাদের দেশে মূলত চার গোত্রের মাহালী রয়েছে : ১. রাজ মাহালী, ২. নাগপুরিয়া, ৩. কলহে, ৪. ভূঞা। রাজমাহালী এবং নাগপুরিয়া মাহালীরা নাগরী ভাষায় কথা বলে। কলহে এবং ভূঞারা আবার আলাদা ভাষায় কথা বলে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে আদিবাসীদের ভাষাগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। যার পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, তবে বৃহত্তর সমাজের প্রভাবটাই বেশি। তবে পৃথিবীর যেকোনো ভাষা শেখা খারাপ কিছু না। প্রয়োজনের তাগিদে সব ভাষা শেখা জরুরি, কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নয়।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলেও আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে সন্তোষজনক কোন গবেষণা এখনো শুরু হয়নি। মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য সরকার চমৎকার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল, সেটাও ঢিলেঢালা ভাবে চলছে। অর্থাৎ শুরু না হতেই সুন্দর একটি উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে।
আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও গৌরবের ঐতিহ্য, যা তারা হাজার বছর ধরে লালন করে আসছে। যেমন, জাতিভেদে প্রতিটি সম্প্রদায়ের রয়েছে আলাদা পোশাক পরিচ্ছদ। সাথে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহারের ইতিহাস। রয়েছে নিজস্ব ভাষায় নৃত্য ও গীত, যা মনকে প্রসন্ন ও অবসাদমুক্ত করে। একই সাথে তাদের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র এবং বাজনার চমৎকার শৈলী রয়েছে। তারা এসব তাদের পূজাপার্বণ, বিয়ে বা সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে।
বিভিন্ন সংস্থা আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের জন্য কাজ করলেও, এখানে আদিবাসীরা পিছিয়ে আছে। দারিদ্রতার কারণে ভালো বাসস্থান নেই, নেই কোন স্বাস্থ্য সচেতনতা। এখনো অনেক মানুষ কিছু হলে ভালো চিকিৎসকের স্মরণাগত না হয়ে কবিরাজের কাছে যায়। অনেক আদিবাসীদের ভালো স্যানিটেশন সম্পর্কে জানা নেই, তারা খোলা মাঠে মলমূত্রত্যাগ করে। অভাব-অনটনের জন্য ছেলেমেয়েরা ভালো জামাকাপড় পরতে পারে না। শিক্ষার হার অনেক কম, ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।
প্রাথমিকে মোটামুটি সাড়া পেলেও ধীরে ধীরে সংখ্যা কমতে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার গুরুত্ব অনেক অভিভাবকগণ এখনো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আদিবাসীরা দরিদ্র, তাই অধিকাংশ আদিবাসীরা কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া বর্তমানে আদিবাসীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সব পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে। তবে পূর্বে আদিবাসীরা শিকার করতেও বেশ পটু ছিল, বর্তমানে বনজঙ্গল পর্যাপ্ত না থাকায় তারা আর শিকার করে না।

তবে উত্তরবঙ্গের মাহালী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনো তাদের পুরোনো পেশা টিকিয়ে রেখেছেন। তাদের প্রধান কাজ মূলত বাঁশ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র তৈরি করা, যা যুগের পর যুগ স্ব-গৌরবে টিকে আছে। তবে আদিবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের পুরোনো পেশা বাদ দিয়ে নতুন পেশার সাথে জড়িত হচ্ছে। এটা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। তাছাড়া অনেকে সরকারি চাকরির দিকেও মনোযোগ দিচ্ছে।
আসুন, সকলে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্ট হই। তাদের হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতি রক্ষায় তাদের পাশে দাঁড়াই। তাহলেই সোনার বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে, কেননা এক অংশকে পেছনে ফেলে রেখে কখনো সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।
জয় খ্রীষ্টফার বিশ্বাস : সাংবাদিক; মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার, বাংলাদেশের খবর
- বাংলাদেশের খবরের মতামত বিভাগে লেখা পাঠান এই মেইলে- bkeditorial247@gmail.com
এমএইচএস