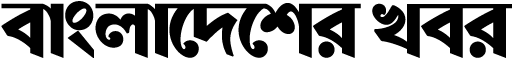বিষয়টা অনেকটা জনপ্রিয় সবজি আলুর মতো। যা সব তরকারিতেই দক্ষতার সঙ্গে মানিয়ে নেয়, স্বাদ অক্ষুণ্ন রেখে। যে কারণে শুধু রাঁধুনিরাই নন, ভোজনরসিকরাও আলু বলতে পাগল। বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির অনিবার্য ‘টার্ম’ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা কনসপিরেসি থিওরির কথা। এটি এতটাই কার্যকরী যে, রাজনীতির যেকোনো ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সমাধান খুঁজে না পেলে অথবা কাউকে সরাসরি দায়ী করার সুযোগ বা ইচ্ছে না থাকলে চোখ বুজে তত্ত্বটি ঘাড়ে চাপানো যায়।
এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বই বলে দেয়, দেশীয় রাজনীতির নাটাই অসীম ক্ষমতাধর কোনো ‘জুজু’র হাতে। যিনি কখনও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়, কখনও দেশের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা বিশেষ শক্তি। যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এমনকি শনাক্তও করা যায় না। অনেকটা জিন-ভূতের মতো রহস্যময়। দেশের জন্ম ইতিহাস থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের সব ঘটনা- এমনকি এই মুহূর্তে রাজনীতির ময়দানে যা ঘটে চলেছে সবকিছুর মূলে ওই অঘটনঘটনপটীয়সী জুজু। অর্থাৎ রাজনীতিতে বিদ্যমান বহুমুখী দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হিংসা-প্রতিহিংসা, সহিংসতা- সবই ব্যাখ্যা করা হয় এই কনসপিরেসি থিওরি দিয়ে।
আধুনিক বিস্ময়কর বিজ্ঞান এখন অবধি ‘থিওরি অব এভরিথিং’ আবিষ্কার করতে না পারলেও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মোড়কে রাজনীতিতে সেই থিওরির জন্ম হয়েছে বহুকাল আগে। দেশীয় রাজনীতির প্রচলিত ধারার মূল দর্শনই হচ্ছে এই তত্ত্ব। যদিও এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোনো ঘটনাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে কল্পনার রং-তুলি দিয়ে রহস্যময় করে তোলার প্রবণতা। তবে রাজনীতিকরা ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয়স্বার্থে খেয়াল খুশিমতো এই তত্ত্বটির প্রয়োগ করে থাকেন।
দেশীয় রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বেপরোয়া প্রয়োগে প্রবীণ রাজনীতিকরা, এমনকি কৌতূহলী জনতা অভ্যস্ত হয়ে পড়লেও নতুন প্রজন্মের কাছে তা সহজবোধ্য নয়। রাজনীতির মোড়কে রহস্যময়, দুর্বোধ্য আর শৈল্পিক ভণ্ডামিকে বুঝতে পারার জটিল চিন্তাভাবনা (ক্রিটিক্যাল থিংকিং) তরুণদের থাকেও না। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বজনীন বয়ান আর নীতি-নৈতিকতা, মানবতার যত সূত্র আছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করেও এই তত্ত্বকে তারা মেলাতে পারেন না। ফলে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির জটিল-কুটিল বোঝাপড়া এড়িয়ে চলতে চায় নতুন প্রজন্ম।
২.
প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর সহাবস্থানও বড্ড গোলমেলে। নিজ নিজ স্বার্থে এসব দল জোট গঠন করলেও সমালোচনার ভাষার কোনো হেরফের নেই। একেকটা দল প্রতিপক্ষকে যে ভাষায় আক্রমণ করে, তা তরুণদের কাছে উদ্ভট, বিস্ময়কর। এমনকি যে নেতাদের ঈশ্বরজ্ঞান করা হয়, প্রতিপক্ষের সমালোচনায় তারাও যে অশালীন শব্দ প্রয়োগ করেন, তা বেশিরভাগ তরুণের রুচি আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমনকি রাজনীতিকদের এমন রুচিহীন বক্তব্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে শোনার যোগ্যও নয়। অথচ অসৌজন্যমূলক শব্দের এমন নির্বিচার ব্যবহার রাজনীতিকরা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।
জাতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর শব্দ প্রয়োগের সংস্কৃতি স্থানীয় নেতারা যেভাবে রপ্ত করেন, তা আরও বিপজ্জনক। এমন শব্দের বেপরোয়া প্রয়োগ পারস্পরিক সম্প্রীতি বা সহাবস্থানকে একেবারেই সাংঘর্ষিক করে তোলে। অনেক সময় রক্তক্ষয়ী সহিংসতাতেও জড়িয়ে পড়েন স্থানীয়রা। রাজনৈতিক এই সংঘাত শেষ অবধি সামাজিক বিভাজনকে উসকে দেয়। যা সামাজিক সম্প্রীতির কাঠামো বিনষ্ট করে শেকড় উপড়ে ফেলে। রাজনীতির এমন বিকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে বড়রা খাপ খাইয়ে নিলেও এ যুগের তরুণরা পারেন না।
৩.
দেশীয় রাজনীতির শেষ কথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যেকোনো কৌশলে, এমনকি বল প্রয়োগ করে হলেও তারা ক্ষমতায় বসতে চায়। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দলগুলো যে দর্শনে শতভাগ আস্থা রাখে সেটা হলো- ‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই’। অর্থাৎ দলীয় স্বার্থে, ক্ষমতার অভিপ্রায়ে তারা নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ পরিবর্তনে সব সময়ই প্রস্তুত। ক্ষমতার লোভে দলগুলো উল্টো আদর্শিক অবস্থানও অনুমোদন করে। ফলে প্রগতিশীলরাও হয়ে উঠতে পারেন রক্ষণশীল, প্রবল বামরাও হয়ে যেতে পারেন ডান। কিংবা ধর্মভিত্তিক দলগুলোও নীতিহীন আচরণ করতে পারে। অর্থাৎ রাজনীতি শব্দটি থেকে ‘নীতি’ বাদ দিয়ে তারা শুধুই ‘রাজ’ করায় বিশ্বাসী।
দলীয় বা গোষ্ঠীস্বার্থে রাজনীতিকদের এমন নীতিহীন হয়ে ওঠা কিংবা দেশীয় রাজনীতির এমন আকস্মিক আদর্শবর্জন প্রবীণরা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিলেও তরুণদের কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। ফলে দেবতাজ্ঞান করা নেতা থেকে শুরু করে প্রান্তিক পর্যায়ে এমন ‘শেষ কথা না থাকা’ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে চরম ধন্দে পড়ে যান তরুণরা। দেশসেবার মুখোশের আড়ালে নীতিহীনতার এমন সংস্কৃতি সমাজের গভীরতর অন্দর পর্যন্ত শেকড় গেড়ে বসে। যেখান থেকে ঘটে নীতিহীনতার সামাজীকিকরণ। সংক্রমিত হয় সরকার, প্রশাসন আর গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো। দুর্নীতি, অনিয়ম, সন্ত্রাসবাদ সমাজে জেঁকে বসে। রাজনীতির এমন বিকৃত, বৈরী, নীতিবর্জিত চেহারা দেখে আঁতকে উঠেন তরুণরা।
শুধু স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতির বিকৃত চেহারাই তরুণদের হতভম্ব করে না, দলগুলোর ভেতরের বিকৃত রূপ আরও ভয়ংকর। যেসব দল গণতন্ত্রের জন্য দশকের পর দশক ধরে লড়াই করার দম্ভ দেখায় তারা নিজেরাই গণতন্ত্র বোঝে না। দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনীতিকরা নীতিগতভাবেই কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরাচারপ্রবণ। একই সঙ্গে তাদের বেশিরভাগই প্রগতির প্রশ্নে রক্ষণশীল, কোনো পরিবর্তনকে সহজে মানতে পারেন না। শীর্ষ নেতাদের বেশিরভাগই ভেতরে ভেতরে পুরানো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থিও। যা তরুণদের আধুনিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রবলভাবে সাংঘর্ষিক।
৪.
দেশীয় রাজনীতির মহান লক্ষ্য বা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জনগণের টেকসই উন্নয়ন। অথচ সেই উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্বশীল নেতাদের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি শুধু বিপজ্জনকই নয়, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা অর্থ অপচয়ের নীল নকশাও বটে। প্রথাগত রাজনীতিকদের উন্নয়ন দর্শন শেষ অবধি পরিবেশ আর জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দেখা দেয়। প্রবলভাবে জনতুষ্টিবাদী এসব রাজনীতিক তাৎক্ষণিক উন্নয়নের চমকে ভোটারদের মুগ্ধ করলেও তাতে সুদূরপ্রসারী বা দীর্ঘমেয়াদে কোনো সুফল থাকে না। তাছাড়া ভোট আদায়ের পরই আমজনতাকে বেমালুম ভুলে নগরমুখী হয়ে পড়েন জনপ্রতিনিধিত্ব করা নেতারা। বড় বড় গেট পেরিয়ে ভোটাররা নেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারেন না। পৌঁছালেও নেতারা চেনেন না। জনসেবার বদলে তারা তখন ভোটের মাঠে খরচ করা টাকা উঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যে প্রবণতা তরুণদের বিস্মিত করে, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে।
ঘরে ঘরে গড়ে তোলা কমিটির নেতাকর্মীদেরই জনগণ ভাবেন রাজনীতিকরা। যাদের আয়ের পথ খুলতে যেকোনো উপায়ের অনুমোদন দেন। এমনকি আমজনতার অর্থ-সম্পদ নানা কৌশলে হাতিয়ে নেওয়া, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, হত্যার মাধ্যমে সমাজে ভীতির সঞ্চার করার ক্ষেত্রেও নীরব সমর্থন দেন। আর সরকার পরিচালনায় আসা রাজনৈতিক দল তো নিজেদেরই রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলে। বিদ্যমান আইন-কানুনের কাঠামো ভেঙে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে হয় নিয়োগবাণিজ্য শুরু করে, নয়তো অনুগতদের পরিচালনায় বসিয়ে শিক্ষা কাঠামো ধ্বংস করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করতেও ছাড়ে না। যা তরুণদের বেড়ে ওঠা, স্বপ্ন দেখা, দেশ ও সমাজের জন্য অবদান রাখার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
এমন দখলবাজিতে রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করেন দলীয় লোকজন। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরির বাজারে কোনো সুবিধা করতে পারেন না সিংহভাগ মেধাবী তরুণ-তরুণী। নিরুপায় হয়ে তারা হয় দেশত্যাগ করেন, নয়তো রাজনীতিকদের দখলে থাকা সরকারি, বেসরকারি চাকরি বা কর্মসংস্থান লাখ লাখ টাকায় কিনতে বাধ্য হন। এতে চরম বৈষম্যের শিকার হতে হয় তরুণদের। গোটা সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে শোষক আর বঞ্চিত শ্রেণিতে। ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলের এমন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপহার পেয়ে শুধু তরুণরাই নন, চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন তাদের পরিবারের সদস্যরাও। যে ক্ষোভ শেষ অবধি গিয়ে পড়ে দল পরিচালনাকারী শীর্ষ নেতাদের ওপর।
৫.
দশকের পর দশক ধরেই ক্ষমতায়িত দলগুলোর হাত ধরে দেশপ্রেমহীন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থপরতার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বন্দোবস্ত গড়ে উঠেছে। যে বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠেছেন তরুণরা। পুঞ্জীভূত সেই ক্ষোভের খানিকটা বিস্ফোরণ ঘটেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে। ইতিহাসে অসামান্য অবদান আর আদর্শের মাহাত্ম্যকে সামনে রেখে ক্ষমতামুখী রাজনীতি সমাজ-রাষ্ট্রে যে বিভাজন আর বৈষম্যের পাহাড় তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধেই রক্ত ঝরিয়েছে তরুণরা। যার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে তরুণদের বহুত্ববাদী রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে ধর্মভিত্তিক এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক লক্ষ্যের বদলে উদার-মানবতাবাদী আকাঙ্ক্ষাও গভীর।
তবে ক্ষমতামুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বার্থে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সর্বজনীন স্পিরিট বহুত্ববাদ থেকে অনেকটা পুরোনো এককেন্দ্রিক গোষ্ঠীবাদী চরিত্রের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। ফলে শিক্ষিত উদ্যমী তরুণদের হাত ধরে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির বড় স্বপ্নের যে রূপরেখা তৈরি হয়েছে, তা বিবর্ণ, বেহাত হওয়ার পথে হাঁটছে। সেটা ঘটছে প্রচলিত ধারার অভিজ্ঞ, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি তাদের অংশীজনদের পরিবর্তনহীন, অতীতমুখী, উল্টোযাত্রার কারণে। রাজনীতির নতুন আকাঙ্ক্ষা ঘিরে প্রবীণদের সঙ্গে তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গিগত দূরত্বের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যাকে বলা যায় রাজনীতির জেনারেশন গ্যাপ।
বস্তুত, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতিতে জ্ঞান-বিস্ফোরণের কারণে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিশাল এক চ্যালেঞ্জের মুখে তরুণরা। মানচিত্রহীন বিশ্বে সেই চ্যালেঞ্জের নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দিচ্ছে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধের নানা উপকরণ, অনুষঙ্গ। রাজনীতির প্রচলিত লেন্স তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পড়তে পারুক, না পারুক তারাই যে আগামীতে দেশ সামলাবেন তা নিশ্চিত। ফলে রাজনীতির প্রচলিত ধারা যত বেশি আধুনিক হবে, পরিবর্তনের সঙ্গে যত বেশি খাপ খাইয়ে নেবে তত বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পরিবেশ তৈরি হবে। যেখানে চালিকা শক্তি হবেন বিপুল প্রাণশক্তির উদ্যমী তরুণ প্রজন্ম। আর তখনই কেবল রাজনীতির জেনারেশন গ্যাপ দূর হবে।
লেখক : সাংবাদিক।